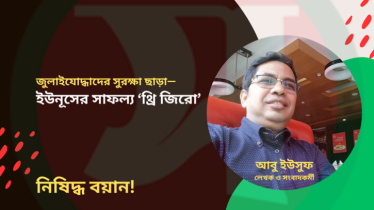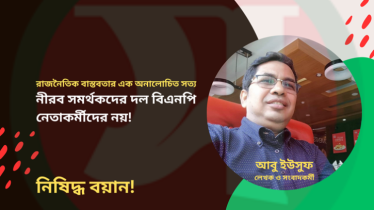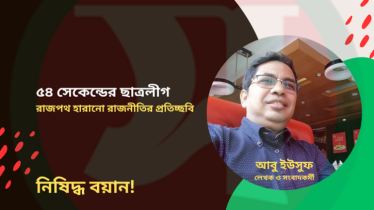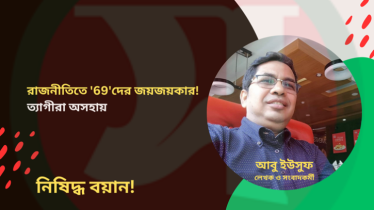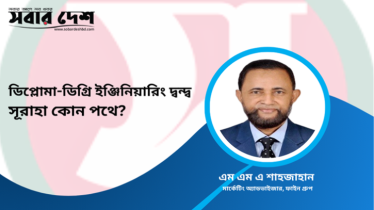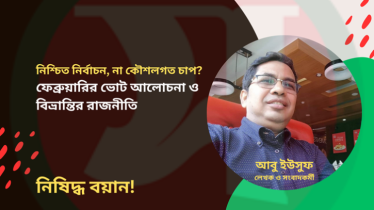বড়াইবাড়ি সীমান্তে বিজয়, ভেতরে ধ্বংস: বিডিআরের শেষ অধ্যায়

২০০১ সালের এপ্রিলে বাংলাদেশের লালমনিরহাট জেলার বড়াইবাড়ি সীমান্তে বাংলাদেশ রাইফেলস (বিডিআর) এবং ভারতের বিএসএফ-এর মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। বিএসএফ অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশে ঢুকে পড়ে। বিডিআর সাহসিকতার সঙ্গে তাদের প্রতিহত করে এবং বহু বিএসএফ সদস্য নিহত হয়। এ বিজয় বাংলাদেশের সীমান্ত রক্ষায় বিডিআরের দৃঢ়তা ও আত্মত্যাগের প্রতীক হয়ে আছে।
‘সীমান্তে বিজয়, ভেতরে ধ্বংস: বিডিআরের শেষ অধ্যায়’ এ শিরোনাম যেমন গর্বের এক স্মৃতিচিহ্ন, তেমনি বয়ে আনে এক রক্তাক্ত ট্র্যাজেডির করুণ প্রতিফলন। বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিডিআর (বাংলাদেশ রাইফেলস) ছিলো সাহস, আত্মত্যাগ ও দেশপ্রেমের প্রতীক। কিন্তু ২০০৯ সালের পিলখানা হত্যাকাণ্ড জাতিকে এক ভয়াবহ ধাক্কা দেয়। বাহিনীর অভ্যন্তরে পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, অব্যবস্থাপনা ও নেতৃত্বের দুর্বলতা এক সময় ভয়ংকর বিস্ফোরণের রূপ নেয়, যা ইতিহাসে এক কালো অধ্যায় হয়ে রয়ে যায়।
এ আলোচনায় আমরা ফিরে তাকাব সেই সন্ধিক্ষণে যেখানে সীমান্তের বীরত্ব ম্লান হয়ে যায় অভ্যন্তরীণ ভাঙনের কাছে।
১. রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা ও বড়াইবাড়ি যুদ্ধের কৌশলগত গুরুত্ব
বড়াইবাড়ি যুদ্ধ শুধুই একটি সীমান্ত সংঘর্ষ নয়; এটি ছিলো একটি কৌশলগত অবস্থান পুনরুদ্ধারের সফল প্রয়াস। ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ-এর আগ্রাসন নিয়ে দীর্ঘদিনের উদ্বেগের প্রেক্ষাপটে বিডিআর স্থানীয় জনসাধারণকে সঙ্গে নিয়ে যে প্রতিরোধ গড়ে তোলে, তা ছিল ‘গণআধারভিত্তিক প্রতিরক্ষা’-এর একটি কার্যকর উদাহরণ। বাংলাদেশের জন্য এটি ছিলো মনোবল বৃদ্ধির প্রতীক, অথচ প্রতিবেশী বৃহৎ রাষ্ট্রের জন্য তা হয়ে দাঁড়ায় কূটনৈতিক অপমানের কারণ।
২. সফলতা থেকে শঙ্কা: ভারতের নিরাপত্তা দৃষ্টিভঙ্গি
বড়াইবাড়ি যুদ্ধের পর ভারতীয় রাজনৈতিক ও সামরিক মহলে বিডিআরের প্রতি এক ধরনের শঙ্কা তৈরি হয়। ছোট অথচ দক্ষ ও মনোবলসম্পন্ন এ বাহিনীকে ঘিরে সীমান্ত নীতিতে দেখা দেয় পরিবর্তন। ভারত ‘proactive deterrence’ নীতি গ্রহণ করে, যার উদ্দেশ্য ছিলো সীমান্তে উত্তেজনা সৃষ্টি করে বাংলাদেশকে রাজনৈতিক ও কূটনৈতিকভাবে চাপে রাখা।
আরও পড়ুন <<>> শিমলা চুক্তি বাতিল: কাশ্মীরের সম্ভাবনা, বাংলাদেশের জন্য শিক্ষা
৩. পিলখানা বিদ্রোহ ও আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপট
২০০৯ সালের ভয়াবহ পিলখানা বিদ্রোহ ঘটে এমন এক সময়, যখন বাংলাদেশে নতুন সরকার দায়িত্ব নিয়েছে এবং ভারতের নির্বাচনী প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এমন সংবেদনশীল প্রেক্ষাপটে একটি রাষ্ট্রীয় বাহিনীর অভ্যন্তরীণ বিদ্রোহ নিছক অভ্যন্তরীণ ক্ষোভ দিয়ে ব্যাখ্যা করা কঠিন। বহু বিশ্লেষকের মতে, দীর্ঘদিনের অবহেলা, বৈষম্য ও সাংগঠনিক দুর্বলতার পাশাপাশি বাইরের প্ররোচনার সম্ভাবনাও একেবারে উড়িয়ে দেয়া যায় না।
৪. বিডিআর: নির্মূল নাকি রূপান্তর?
বিডিআর বিদ্রোহের পর যে কাঠামোগত পরিবর্তন আসে, তা বাহিনীটির এক ধরনের ‘পুনর্জন্ম’। নাম বদল, প্রশিক্ষণ পদ্ধতির আধুনিকায়ন, নেতৃত্বে সেনাবাহিনীর প্রভাব বৃদ্ধি এসবকিছু মিলিয়ে এটি ‘নির্মূল’ না হলেও ‘পুনর্গঠন’ বলা চলে। তবু অনেকের মতে, একটি ঐতিহ্যবাহী বাহিনীর এমন বিলুপ্তি ছিলো একটি পরিকল্পিত কৌশল, যাতে ভবিষ্যতে এ স্বাধীনচেতা বাহিনী রাষ্ট্রের জন্য হুমকি না হয়ে ওঠে।
৫. মিডিয়া ও রাজনৈতিক ন্যারেটিভ
পিলখানা বিদ্রোহের পর রাষ্ট্রীয় ও প্রধানধারার গণমাধ্যমে বিডিআর-এর বিরুদ্ধে জনমত তৈরি করা হয়। ‘বিশ্বাসঘাতক’ ও ‘রাষ্ট্রদ্রোহী’ হিসেবে চিত্রিত করে তাদের বীরত্বগাথা প্রায় মুছে ফেলার প্রয়াস চলে। এক সময়ের সীমান্ত রক্ষাকারী বাহিনীকে ইতিহাস থেকে প্রায় বিলুপ্ত করার এ প্রচেষ্টা নিয়ে বিতর্ক এখনও বিদ্যমান।
বড়াইবাড়ি যুদ্ধ এবং বিডিআরের পতন দুটো ঘটনা সরাসরি সম্পর্কযুক্ত না হলেও, সময়, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট এবং আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করলে একটি গভীর যোগসূত্র স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ইতিহাস একদিন হয়তো নির্ধারণ করবে বিডিআর কেবল একটি বাহিনী ছিলো না; এটি ছিলো প্রতিরোধ, আত্মত্যাগ ও অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রতীক। প্রশ্ন রয়ে যাবে: এটি কি ছিল কৌশলগত ব্যর্থতা, নাকি একটি সফল বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণে আনার জন্য গভীর পরিকল্পনার অংশ?
লেখক:
বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের আইনজীবী ও
রাজনৈতিক বিশ্লেষক।